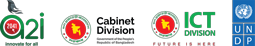-
-
প্রথম পাতা
-
-
- উপজেলা সম্পর্কিত
-
উপজেলা পরিষদ
উপজেলা স্থায়ী কমিটি সমূহ
-
উপজেলা স্থায়ী কমিটি সমূহের সদস্যদের তালিকা
-
আইন-শৃঙ্খলা স্থায়ী কমিটি
-
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো স্থায়ী কমিটি
-
কৃষি ও সেচ স্থায়ী কমিটি
-
মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্থায়ী কমিটি
-
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা স্থায়ী কমিটি
-
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থায়ী কমিটি
-
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
-
যুব ও ক্রীড়া স্থায়ী কমিটি
-
সমাজকল্যাণ স্থায়ী কমিটি
-
মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
-
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ স্থায়ী কমিটি
-
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় স্থায়ী কমিটি
-
সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
-
পরিবেশ ও বন স্থায়ী কমিটি
-
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটি
-
অর্থ, বাজেট ও পরিকল্পনা স্থায়ী কমিটি
-
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি স্থায়ী কমিটি
-
উপজেলা স্থায়ী কমিটি সমূহের সদস্যদের তালিকা
-
উপজেলা প্রশাসন
- সরকারী অফিস
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
- ই-সেবা
- গ্যালারী
মেনু নির্বাচন করুন
-
-
প্রথম পাতা
-
-
-
উপজেলা সম্পর্কিত
উপজেলা পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
-
উপজেলা পরিষদ
পরিষদ
কার্যবিবরণী
বাজেট
উপজেলা পরিষদের সম্পদ
উপজেলা স্থায়ী কমিটি সমূহ
- উপজেলা স্থায়ী কমিটি সমূহের সদস্যদের তালিকা
- আইন-শৃঙ্খলা স্থায়ী কমিটি
- যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো স্থায়ী কমিটি
- কৃষি ও সেচ স্থায়ী কমিটি
- মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্থায়ী কমিটি
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা স্থায়ী কমিটি
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থায়ী কমিটি
- মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
- যুব ও ক্রীড়া স্থায়ী কমিটি
- সমাজকল্যাণ স্থায়ী কমিটি
- মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ স্থায়ী কমিটি
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় স্থায়ী কমিটি
- সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- পরিবেশ ও বন স্থায়ী কমিটি
- বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটি
- অর্থ, বাজেট ও পরিকল্পনা স্থায়ী কমিটি
- জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি স্থায়ী কমিটি
-
উপজেলা প্রশাসন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউ এন ও এর কার্যালয়
সংগঠন সম্পর্কিত
সেবা ও অন্যান্য
-
সরকারী অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক
কৃষি, মৎস্য, প্রাণি ও খাদ্য বিষয়ক
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র
- ই-সেবা
-
গ্যালারী
ফটো গ্যালারী
ভিডিও গ্যালারী
Main Comtent Skiped
শিরোনাম
কান্তজীউ মন্দির
স্থান
দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং কাহারোল উপজেলা সদর থেকে ৬ মাইল পূর্বে দিনাজপুর-পঞ্চগড় সড়কের পশ্চিমে ঢেপা নদীর পাড়ে এক শান্ত নিভৃতগ্রাম কান্তনগরে এ মন্দিরটি স্থাপিত।
কিভাবে যাওয়া যায়
দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং কাহারোল উপজেলা সদর থেকে ৬ মাইল পূর্বে দিনাজপুর-পঞ্চগড় সড়কের পশ্চিমে ঢেপা নদীর পাড়ে এক শান্ত নিভৃতগ্রাম কান্তনগরে এ মন্দিরটি স্থাপিত।দিনাজপুর থেকে বাসযোগে যাওয়া যায়।
যোগাযোগ
0
বিস্তারিত
অবস্থান ঃ
কান্তজিউ মন্দির বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ২৬৬ টি পোড়ামাটির অলঙ্কৃত মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে সুন্দরতম নিদর্শন। দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ৬ নং রামচন্দ্র ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রাম ও ৩ নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের মুকুন্দপুর গ্রামের শেষ সীমানায় ৫ নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তনগর গ্রামে শ্রী শ্রী কান্তজীউ মন্দিরটি তিনশত বছরেরও বেশি সময় ধরে সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। দিনাজপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ২০ কিমি. উত্তরে, কাহারোল উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার পূর্বে এবং দিনাজপুর-তেতুঁলিয়া মহাসড়কের প্রায় ১ কিমি. পশ্চিমে পূণর্ভবা/ঢেঁপা নদীর পশ্চিম তীরে কান্তনগর গ্রামে এই মন্দিরটি স্থাপিত।
মন্দিরের নামকরণ ঃ
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নামের মধ্যে শ্রীকান্ত (রুক্সিনীকান্ত) একটি নাম। তাই মহারাজা প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের কান্ত নাম অনুসারে মন্দিরটির নাম রাখেন কান্তজিউ মন্দির। অর্থাৎ কান্ত হচ্ছে কৃষ্ণের নাম আর জীউ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরের নামানুসারে সেই গ্রামটির নাম রাখা হয় কান্তনগর। কান্তনগর গ্রামটি ছিল দ্বীপের মতো। এর চারপাশে ঢেঁপা নদী প্রবাহিত ছিল। মন্দির নির্মাাণের পূর্বে এখানে জনবসতি ছিল না। মহারাজা প্রাণনাথ শুধু একজন দক্ষ শাসক ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন নির্জন ধার্মিক। তাই তিনি শ্রী কৃষ্ণের আরাধনা ও পুজার্চনা করার জন্য এমন একটি নির্জন জঙ্গলার্কীণ দ্বীপকে বেছে নেন। কারণ প্রাচীনকালে মুণী-ঝষিরাও এরকম নির্জন ও গভীর অরণ্যে তপস্যা করতেন।
পরিচিতি ঃ
দিনাজপুরের প্রখ্যাত জমিদার প্রাণনাথ ও তাঁর পোষ্যপূত্র রামনাথ ১৭০৪-১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পঞ্চাশ ফুট বর্গাকৃতির ত্রিতল বিশিষ্ট ইটের তৈরি এ মন্দিরটি একটি উচুঁ মঞ্চের উপর নির্মিত। এটি একটি নবরতœ মন্দির। মন্দিরের নিচ তলার ছাদ ও দ্বিতলের ছাদের চার কোণে চারটি করে আটটি অলংকৃত চুড়া বা রতœ এবং ত্রিতলের ছাদের মধ্যস্থলে আছে বৃহদাকার কেন্দীয় চুড়ার ধবংসাবশেষ। মন্দিরের সর্ম্পূণ বহিগাত্রে পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট ফলকচিত্রের অলংকরণে সুশোভিত। এসব ফলকচিত্রে উদ্ভিদ, প্রাণীকুল, জ্যামিতিক নকশা, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌরাণিক দৃশ্যাবলি এবং তদানীন্তন সামাজিক ও অবসর বিনোদনের চমৎকার দৃশ্য খচিত রয়েছে। মন্দিরের নীচ তলার গর্ভগৃহে কান্তজিউ বিগ্রহ স্থাপিত।
১৯৬০ ইং সালে কান্তনগর মন্দির সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্তি হিসেবে ঘোষণার পর থেকে প্রতœতত্ত¡ বিভাগ এর আবশ্যকীয় সংস্কার এবং সংরক্ষণ কার্যাদি সম্পাদন করছে।
১৬০৮ সালে দিনাজপুরের রাজবংশের প্রথম রাজা শ্রীমন্ত দত্ত রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। যা প্রায় সাড়ে তিনশত বছর স্থায়ী হয়েছিল। দিনাজপুর রাজ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রাণনাথ শ্যামগড় (বর্তমান নাম কান্তনগর) নামক এক দ্বীপের মতো নির্জন জায়গায় বাংলার স্থাপত্যের গর্ব শ্রী শ্রী কান্তজিউ মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় ১৭০৪ খ্রি.। রাজা প্রাণনাথ বেঁেচ থাকতে মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। তাই তার দত্তক পূত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রি. মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে বিগ্রহ স্থাপন করেন। অপূর্ব সুন্দর অতুলনীয় রুপে শ্রী শ্রী কান্তজীউ মন্দিরের গায়ে আছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকচিত্র। ফলকচিত্রগুলোর মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত সহ অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা আছে।
মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য ঃ
দিল্লীর স¤্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক মহারাজা উপাধি দেওয়ায় প্রাণনাথের প্রাণ ভরে যায়। তাই তিনি ধর্মোদ্দেশ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সময় কিছুদিনের জন্য শ্রী বৃন্দাবনে তীর্থে যান। রাজা প্রাণনাথ ছিলেন আর্দশ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং পরম কৃষ্ণ উপাসক। শ্রী বৃন্দাবনে রাধামাধব শ্রী রুক্সিনীকান্তের মন্দিরের বিগ্রহ দেখে রাজা খবুই মুগ্ধ হন এবং তাঁর মনে সাধ হয় ঐরুপ তিনি তাঁর নিজ দেশে মন্দির তৈরি করে পূজা অর্চনা করেবন। বৃন্দাবনের রাধামাধব রুক্সিনীকান্ত মন্দিরের বিগ্রহের মতই অনেক কষ্টে অধিক অর্থের বিনিময়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সংগ্রহ করেন। শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পেয়ে রাজা আনন্দিত মনে নৌপথে বিগ্রহ নিয়ে দিনাজপুরাভিমুখী রওয়ানা হন। নৌকা নদীর ¯্রােতে ভাসতে ভাসতে গঙ্গার পথ বেয়ে বাংলাদেশের সীমানায় এসে পদ্মার বুকে পড়ে। তারপর মহানন্দার পথ ধরে উত্তর দিকে এসে পূণর্ভবা নদীর ¯্রােতধারায় পড়ে। অবশেষে নৌবহর দিনাজপুর শহর, রাজবাটি কতগ্রাম কত প্রান্তর অতিক্রম করে ঢেঁপা নদীর তীরে কান্তনগর নামক স্থানে (পূর্বনাম শ্যামগড়) এসে থেমে যায়। মহারাজা প্রাণনাথ এখানেই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তবে রাজার মনে যে আশা আকাঙ্খা ছিল তা ক্রমে গভীর দুঃশ্চিন্তায় মগ্ন হয়। তিনি চেয়েছিলেন মাঝে মাঝে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ নিজ রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে পূজার্চনা করবেন। তাই ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথী উপলক্ষে আগের দিন নদী পথে নৌকার করে বাদ্য বাজনা সহকারে শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দিনাজপুর রাজবাড়ি মন্দিরে নিয়ে যান এবং কার্তিক মাসের চাঁদের পূর্ণিমা তিথীর আগের দিন শ্রীকৃষ্ণের (কান্ত) বিগ্রহ নিজ মন্দিরে ফিরে আনা হয়। সেই সময়ের চিরাচরিত নিয়ম আজও চলছে। মহারাজা প্রাণনাথ বেচেঁ থাকতে মন্দিরের কাজ শেষ করতে পারেন নাই। তাই আর দত্তকপুত্র ও রাজার একমাত্র উত্তরাধিকারী পরবর্তী রাজা রামনাথ ১৭৫২ খ্রি. মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।
মন্দিরের নির্মাণ সামগ্রী ঃ
শ্রী শ্রী কান্তজিউ মন্দিরটি ইট সুড়কি ও পাথর দিয়ে তৈরি শুধুমাত্র দরজাগুলো কাঠের তৈরি। স্থানীয় নদী ও পুকুরের এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ইট ও টেরাকোটাগুলো। ইট ও টেরাকোটাগুলো আগুনে পোড়ানো রক্তের মতো লালবর্ণ। এ সমস্ত ইট ও টেরাকোটাগুলো স্থানীয় গ্রাম্য মিস্ত্রি ও কারিগর তৈরি করেছেন। মন্দিরটি ৩ ফুট উচুঁ বেদীর উপর নির্মিত। অপুর্ব সুন্দর এই বেদীটি পাথর দিয়ে তৈরি। মুল মন্দিরটির ভিত্তি ও দেওয়াল সুদৃঢ় করার জন্য কঠিন পাথর দিয়ে বেদীটি তৈরি করা হয়েছে। স্থাপত্যটি স্থায়ীত্বপূর্ণ করার জন্য সুকৌশলে এই বেদীটি তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দিরটি তৎকালীন প্রকৌশল বিদ্যার অন্যতম কীর্তি যা আধুনিক প্রকৌশলীদের অনুপ্রেরণার উৎস। কান্তজিউ মন্দির ইট ও টেরাকোটাগুলো স্থানীয় নদী ও পুকুরের এটেঁল মাটি দিয়ে তৈরি করা হলেও এর ভিত্তির পাথরগুলো স্থানীয় নয়। কারণ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সে সময় পাথর উৎপন্ন করা হতো না। এই পাথরগুলো হিমালয়ের তড়াই অঞ্চল, আসামের পার্বত্যদেশ, বিহারের রাজমহল পাহাড় ও বিন্ধ্যাঞ্চল পার্বত্য এলাকা থেকে আমদানী করা হয়।
টেরাকোটার শিল্প ঃ
অসংখ্য প্রাচীন প্যাগোডা, মন্দির ও মসজিদের অধিষ্ঠানভুমি এই বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক পড়োভুমির বাংলাদেশের মধ্যে দিনাজপুর জেলা প্রতœখনি নামে পরিচিত আছে। মন্দিরের মহিমা ও মাহাত্বে কান্তজীউ মন্দির অনন্যপূর্ণ পবিত্র মন্দির। দেশ-বিদেশে অসংখ্য নর-নারীর কাছে মন্দিরটি পরম পবিত্র ও জাগ্রত তীথক্ষেত্র। তার চেয়ে পোড়ামাটির ফলকের চিত্রগুলো আরো বেশি জাগ্রত পর্যটকদের কাছে। মন্দিরের চার দেওয়ালে শাস্ত্রীয় চার যুগের কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা আছে। মন্দিরের নিচ হতে দ্বিতীয় সারিতে চারপাশে মুঘল আামলের চিত্র দেখা যায়। মুঘল আমলের নৌযাত্রা, হাতি, গন্ডার, মুঘল অস্ত্রধারী সৈনিক, রাজা-বাদশা প্রভৃতি চিত্র আছে। তাছাড়া উটের পিঠে চড়ে ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়ে বাঘ শিকার, গজারোহীর পশুশিকার, জীব-জন্তুর লড়াই, মৃগয়া শিকারী, বাঘের কবলে অসহায় শিকারী, বাজপাখি, ভাড়সহ গোয়ালা, নৌকার মাঝি, পালকির বেহারা, সন্ন্যাসী, পালকি ভ্রমণ প্রভৃতি সামাজিক জীবনের খন্ডচিত্র দেখা যায়। শাস্ত্রীয় চারযুগ হচ্ছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে নারায়ণ, ত্রেতার রাম ধনুকধারী, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মন্দিরের উপরের অংশে দক্ষিণ দিকে আছে সত্য যুগের ঘটনা। যেমন- নারায়ণ চন্ডী বা কালী যুদ্ধ। মন্দিরের উত্তর দিকে আছে ত্রেতা যুগের ঘটনা। যেমন- রাম-রাবন যুদ্ধ, ভীষ্ম ও কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, লংকা কান্ড, হনুমানের পিঠে রাম-লক্ষণ, মেঘনাধবধ দৃশ্য। অতি সূক্ষè অনুভুতি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায যে, গ্রামীণ স্থপতি ও শিল্পীদের পোড়ামাটির ফলকের তৈরি সাক্ষাৎ লংকা কান্ড। পূর্ব দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকের মাধ্যমে দ্বাপর যুগের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- শয্যাশায়ী ভীষ্ম, পরশুরামের নিক্ষত্রীয়করণ যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অর্থাৎ কৌরব বংশ ও পান্ডব বংশের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে গান্ধরীর একশত পুত্রের মৃত্যু হয়, আর পান্ড বংশের জয় হয়। ভয়াবহ বীরবিক্রমে পরিপূর্ণ রক্তরঞ্জিত এই যুদ্ধের দৃশ্য দেখলে মনে হয় যে সাক্ষাত কুরুক্ষেত্র।
মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে যে পোড়ামাটির ফলক আছে তা হচ্ছে কলি যুগের বর্ণনা। যেমন- কলিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। টেরাকোটার পাচঁটি চক্রে রাধা কৃষ্ণ মূর্তি ও ষোলশত গোপী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা। পৌরাণিক জীবনাশ্রিত টেরাকোটাগুলোর গভীরে নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে অজান্তে কৌতুহলী দর্শকের মনে রামায়ণ, মহাভারত ও অসংখ্য পুরাণের ঘটনার ভীরে হারিয়ে যায়। প্রেমিক ও নায়ক বেশী শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখে ভক্ত মনে সম্বিত হারিয়ে যায়। মথুরা বৃন্দাবনের পতে কোন অজানা অপার্থিব স্বপ্নময় জগতে। পোড়ামাটির ফলকে কান্তজিউ মন্দিরের দেয়ালগুলো আবৃত আছে। একটু জায়গাও ফাকাঁ নেই। শুধু পৌরাণিক কাহিনীই চিত্রিত হয়নি অসংখ্য ফুল, লতা-পাতা, পশু-পাখি ও জ্যামিতিক নকশাও আছে। অসংখ্য খন্ড খন্ড পোড়ামাটির ফলকে সাজানো আছে পৌরাণিক কাহিনী। কতগুলো যে খন্ড বা চিত্র আছে তা বলা মুশকিল এমন কি প্রতিটি চিত্রের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে প্রায় কয়েক দশক লেগে যেতে পারে। তারপরও সব চিত্রের কাহিনী খুঁেজ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। গ্রামীণ স্থপতিরা এমন মনের মাধুরী মিশিয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন যেন মনে হয়, মানুষ ও প্রকৃতি ্একত্রিত হয়ে অপরুপ এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।
মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে নিচ হতে দ্বিতীয় সারিতে মহাভারতের কাহিনী শুরু। যেমন- শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্য জীবন, ননী চুরী, রাক্ষসী বধ, কং সবধ প্রভৃতি। দক্ষিণ পূর্ব কোণে নিচ হতে দ্বিতীয় সারিতে রামায়ণের কাহিনী শুরু। যথাক্রমে রাজা দশরথের তিন স্ত্রী কৌশলা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। তারপর রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রæঘœ এর জন্ম রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুণির পুত্র সিদ্ধমণিকে শর নিক্ষেপ করে হত্যা ও লাশ বহন। তারকা রাক্ষসী বধ, কনে সাাজিয়ে সীতাকে দেখানো হচ্ছে, রামের হর ধনু ভঙ্গ, ক্রমান্বয়ে রাম সীতাসহ রামের অন্যান্য তিন ভাইয়ের বিয়ে। অসুস্থ রাজা দশরথের রাম সীতা ও লক্ষণকে পঞ্চবটি বনে নিয়ে যাচ্ছে, লক্ষণ কর্তৃক সুপর্ণখার নাসিকা কর্তন, পূর্ব দেওয়ালের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে গন্ডি রেখার মধ্যে সীতা রাবন কর্তৃক সীতা হরণ, রাবণকে বাধা দিচ্ছে জটায়ু পাখি লংকার অশোক বনে সীতা, সুগ্রীবের সাথে রামের বন্ধুত্ব, রামের এক বাণে সপ্ত তাল গাছ ভেদ, সুগ্রীবের সাথে বালীর যুদ্ধ, রামের চরণে হনুমানের প্রণাম, সমুদ্রে সেতু নির্মাণ প্রভৃতি চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা আছে। চিত্রগুলি ব্যাখ্যা করে দেখলে মনে হয় এটি শুধু মন্দির স্থাপত্য নয়, এটি একটি ইটে লেখা মহাকাব্য অথবা পোড়ামাটির ফলকে নির্মিত একখানি সার্থক মহাকাব্য। রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে অনেক। কিন্তু মনে হয় কান্তজিউ মন্দিরের ছবিগুলো দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত কাহিনী নিয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।
মন্দিরে শিলালিপি ঃ
প্রত্যেকটি স্থাপত্যের শিলালিপি থাকে। কান্তজিউ মন্দিরের তেমনি আছে ভিত্তিদেশের উত্তর দিকে একটি শিলালিপি। শিলালিপির রচনাশৈলী যেমন পান্ডিত্যপূর্ণ তেমনি রহস্য জনকও বটে। শিলালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত- শ্রী শ্রী কান্ত-
শাকে বেদাব্দি কাল ক্ষিতি পরিগণিতে ভুমিপ; প্রাণনাথ:
প্রাসাদাঞ্চতিরম্য সুরচিত নবরতœাখ্য মস্মিন্যকার্ষীৎ
রুক্সিন্য: কান্ত তুষ্ঠো সমুদিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্ত কান্তায় কান্তস্য তু-নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌ:
বাংলায় অনুবাদ ঃ
রাজা প্রাণনাথ অতি সুন্দর প্রাসদতুল্য সুরচিত মনোরম নয়টি রতœচূড়া বিশিষ্ট শ্রী শ্রী কান্তজীউ মন্দিরটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পিতার সংকল্প, সিদ্ধির জন্য রাজা রামনাথ শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুসারে এই মন্দিরের নাম কান্তজীউ মন্দির রেখে সংকল্প সমাপ্ত করেন।
মন্দির নির্মাণের সময়কাল ঃ
মহারাজা প্রাণনাথ ১৭০৪ খ্রি. এই মন্দিও নির্মাণের শুরু করেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর পোষ্যপুত্র রাজা রামনাথ মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করে ১৭৫২ খ্রি.। মন্দিরটি নির্মাণ করতে সময় লাগে প্রায় ৪৮ বছর।
নবরতœ মন্দির ঃ
নয়টি চুড়া শোভিত মন্দিরকে বলা হয় নবরতœ মন্দির। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে নবরতœাখ্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে ১৮৯৭ খ্রি. প্রচন্ড ভুমিকম্পে মন্দিরের রতœচুড়াগুলো ভেঙ্গে যায়। প্রথম তলার চার কোণে চারটি, দ্বিতীয় তলার চারকোণে চারটি এবং তৃতীয় তলার মুলচুড়াসহ মোট নয়টি চূড়া ছিল। শীর্ষ চূড়ায় সংস্থাপিত ছিল একটি ধর্ম পতাকা। ধর্মপতাকটি ছিল পিতলের তৈরি যা উচ্চতায় ছিল ১২ (বার) ফুট এবং ওজন ছিল প্রায় ৭ মণ।
আয়তন ঃ
কান্তজিউ মন্দিরটি চতুর্ভুজ। প্রতিটি দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট। পাষানযুক্ত বেদীটি সমতল ভুমি থেকে ৩ ফুট উচুঁ এবং এর বিস্তার ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। চারকোণা মন্দিরটি সমতল প্রঙ্গণ থেকে সর্বোচ্চ শীর্ষদেশের উচ্চতা ৭০ ফুট।
রাসমেলা ঃ
কান্তজিউ মন্দির ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এর একটি। এই মন্দিরকে নিয়ে গড়ে উঠে র্তীথ মেলা। প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীতে রাসলীলা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা উপলক্ষ্যে শুরু হয় মাসব্যাপী রাসমেলা ধর্মীয় সমারোহপূর্ণ রাসমেলায় হাজার হাজার র্তীথ যাত্রির সমাগম হয়। সারাদিন ধরে পিপীলিকার সারির মত সংকীর্ণ মেঠোপথ ধরে, কেউবা মোটর বাসে কেউবা রিক্সায় বা ভ্যানে আবার কেউ বা ভটভটি, নসিমনে চড়ে নানা গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তীর্থযাত্রীগণ এগিয়ে আসে মন্দিরের দিকে। তীর্থযাত্রীদের কাছে বছরের মধ্যে এই দিনটিই মহাপবিত্র দিন। সেদিন গভীর রাতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে বাদ্য বাজনা সহকারে কীর্তন গাইতে গাইতে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরের শতাধিক গজ পশ্চিমে রাসমঞ্চে। রাসপূজা চলাকালীন সময়ে ঢোল বাশির বাজনায় ও মা বোনদের উলু ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসে ও দাঁড়িয়ে থাকে তীর্থযাত্রীরা। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা ও প্রেমলীলার রুপ দেখে অদ্ভুত শিহরণ জাগে ভক্তদের মনে। ধীরে ধীরে রাত কেটে যায়। পূণ্যার্থীরা গৃহামুখী হয়। তারপর প্রায় একমাস চলে কেনা-বেচার মেলা। যেমন- গুড়ের জিলাপী, মিষ্টির দোকান, মুনহারী, শাখা-সিদুর, জুতা, কাপড়, ছেলে-মেয়েদের খেলনার দোকান, ফার্নিচার ইত্যাদি। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য থাকে সার্কাস, মোটর সাইকেল খেলা, নাগরদোলা, যাত্রা।
¯œানযাত্রা ঃ
বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদের পূর্ণিমার তিথীতে শ্রীকৃষ্ণের ¯œান উৎসব হয়। শ্রীকৃষ্ণের ¯œান উৎসব দেখার জন্য হাজার হাজার ভক্ত ভোর না হতেই চলে আসে। ভক্তদের উপচেপড়া ভীড়ে তিল পরিমাণ জায়গা থাকে না। ভক্তদের মাঝে শুরু হয় প্রতিযোগিতা কে সবচেয়ে কাছাকাছি থেকে শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ ঘটি জল দিয়ে ¯œান করা দৃশ্য উপভোগ করতে পারে। কথিত আছে যে, শ্রী কৃষ্ণের ¯œান দেখলে অনেক পূণ্য হয়। তাই পূর্ণার্থীরা শত শত মাইল থেকে ছুটে আসে। বিভিন্ন বাদ্য বাজনা ও মা-বোনদের উলু ধবনিতে মুখরিত হয়ে উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গন। এ দৃশ্য দেখলে আনন্দে পুলকিত হতে হয়। কবি গুরুর ভাষায়, হৃদয় আজি নাচে আমার, ময়ুয়ের মতো নাচে রে। মনে হয় এই দিনটি একটি স্বর্গীয় দিন। পঞ্জিকার মতে ¯œানের দিনক্ষণ ঠিক হয়। কোনো কোনো বছর জ্যৈষ্ঠ্যের শেষাশেষি আবার কোন বছর আষাঢ়ের প্রথম ভাগে ¯œান উৎসব হয়। ভক্তদের এতো বেশি ভীড় যে, প্রতিযোগিতা করে নৌকায় ওঠে। ফলে ঐদিন যে কত বার নৌকাডুবি হয়ে তার হিসাব নেই।
শিবরাত্রী ব্রত ঃ
প্রতি বছর মাঘ মাসের কৃঞ্চপক্ষের চর্তুদশ তিথীতে শিবরাত্রি ব্রত পালিত হয়। দুর দুরান্তের মা-বোনেরা সারাদিন উপোস থেকে সারারাত জেগে বাবা ভোলানাথের পুজার্চনা করে। পুজার্চনার মধ্যে মা-বোনেরা বাবা ভোলানাথের কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। কুমারী মেয়েরা বর প্রার্থনা করে যেন তাঁর মতো একজন গুনবান পতি পায়। দিবস শেষ না হতেই মা-বোনেরা মন্দিরে এসে শিব ভোলানাথের পুজার্চনা শুরু করে। সারারাত ধরে চলে কীর্তন। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে শিব মন্দির অবস্থিত।
তারকব্রক্ষ নামযজ্ঞানুষ্ঠান ঃ
প্রতি বছর বৈশাখ মাসের চাঁদের পুর্ণিমা তিথীতের অর্থাৎ বৌদ্ধ পুর্ণিমায় শুরু হয় ২৪ প্রহর ব্যাপী (বর্তমানে ৪০ প্রহর) তারকব্রক্ষ নামযজ্ঞানুষ্ঠান। ঘরি, কৃষ্ণ, রাম। তিন যুগের তিনটি নামই হলো কলি যুগের একমাত্র মুক্তির প্রাণ। তাই এই নামশুধা শ্রবণ করতে দুর-দুরান্তের হাজার হাজার ভক্তমন্ডলী ছুটে আসে মন্দির প্রাঙ্গণে।একনাথ শ্রবণ করতে করতে ভক্তরা ব্যকুল হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। মুখে কেবল ‘কৃষ্ণ’ নাম আর নয়নে অশ্রæ নিয়ে আকুল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকে।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।
স্থানীয় ও দুর দুরান্ত হতে নাম সংকীতনের দলে আসে নাম সুধা বিতরণ করতে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিন দিন রাত্রি (বর্তমানে ৫ দিন ৫ রাত্রি) পর শেষ হয়ে যায় এই ভবের মেলা।
দোলপূর্ণিমা ঃ
অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনর মধ্যে কান্তনগরেও দোল পুর্ণিমা পালিত হয়। ফাল্গুন মাসে চাঁদের পুর্ণিমার তিথীতে দোল পুর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুর্ণিমাকে গৌড় পুর্ণিমা বলে। তার পর দিন থেকে পুর্ণিমা পুর্ব দিন অর্থাৎ চর্তুদশ তিথীতে ভেরার ঘরে (মেরার ঘর) আগুন জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তার পর দিন থেকে শুরু হয় আবীর (হলি) ছিটিয়ে দোল উৎসব।
নৌবিহারে রাজবাড়ি গমন ও প্রত্যাগমন ঃ
কান্তজিউ বিগ্রহ নয় মাস কান্তজিউ মন্দিরে অবস্থান করে। বাকি তিন মাস দিনাজপুর শহরের রাজবাড়িতে অবস্থান করে। জন্মাষ্ঠমীর দুই/একদিন আগে কান্তজিউ বিগ্রহ নৌকা যোগে নদীপথে রাজবাড়ি গমন করে। এই দিনে হাজার হাজার ভক্তমন্ডলী তিন মাসের বিদায় যাত্রায় সমবেত হন। কেউবা নিজের গাছের নারকেল, কেউবা বাতাবি লেবু, কেউবা লাউ-কুমড়া, কেউ দুধ অর্থাৎ কোনো না কোনো ফল-মুল নিয়ে যায় নদীর ঘাটে। এই সমস্ত দ্রবাদি দিয়ে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে বিদায়ের শেষ শ্রদ্ধা জানায়। হরিবল আর উলু ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে যায় নদী ঘাট। বৈষ্ণব মরমী সাধকরা র্কীতন করে আর চলে নানা রকম বাদ্য-বাজনা। সঙ্গে থাকে পুলিশ প্রশাসন। কোনো নৌকায় বাজে মাইক, কোনো নৌকায় থাকে পুলিশ, কোনো নৌকায় থাকে ম্যাজিস্ট্রেট। কোনো নৌকায় বৈষ্ণব মরমী সাধকরা র্কীতন করে। কান্তজিউ বিগ্রহের নৌকা ফুলে ফুলে সাজানো হয়। আবার অনেক নৌকার ভক্তদের আনন্দ চলে সারাক্ষণ। ছোট বড় ছেলে-মেয়েরা নদীতে নামে ¯œান করতে। তারা ঠাকুরের সঙ্গে নদীর স্রোতে ভেসে যায় অনেক দুর। তাদের কাছে এই দিনটি একটি স্বরণীয় দিন। এই দিনে তাদের হারিয়ে যেতে নেই মানা। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে প্রসাদ নেওয়ার ধুম পরে যায়। কেউ একবার প্রসাদ পায় না, আবার কেউ পেট পুরে প্রসাদ খায়। অনেকে নৌকা ভাড়া করে ঠাকুরের সাথে রাজবাড়ি যায়। প্রায় ৩০-৪০ খানা নৌকা সহযাত্রী হিসেবে যায়। নদীর ঘাটে ঘাটে অধীর আগ্রহে ভক্তবৃন্দরা অপেক্ষা করে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে বিদায় দেয়ার জন্য। এভাবে সারাদিন ধরে নৌকায় করে কাঞ্চন ব্রীজে গিয়ে নৌকা থামে। কাঞ্চন ব্রীজে কান্তজিউ বিগ্রহ নৌকা থেকে নামানো হয়। সেখানে অপেক্ষা কওে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ। র্কীতন গাইতে গাইতে এবং হরেক রকম বাদ্য বাজনা বাজিয়ে কড়া নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে কান্তজিউ বিগ্রহ নিয়ে যাওয়ার হয় রাজবাড়ি। কাঞ্চন ঘাট থেকে রাজবাড়ি যাওয়ার রাস্তার দুইধারে নান রকম আলাক সজ্জা থাকে। আলোক সজ্জার মধ্যে সব থেকে মনোরম হচ্ছে মইবাতি। কান্তজিউ বিগ্রহের সাথে পথ চলতে চলতে ভক্তরাও বিমূঢ় হয়ে যায়। তখন মনে হয় যেন স্বর্গের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। রাজবাড়িতে তিন মাস অবস্থান করার পর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীর দুই/এক দিন আগে পালকিযোগে রাজপথ দিয়ে নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। তারপর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীতে শুরু হয় রাসযাত্রা।
নিত্যদিনের পূজার্চনা ঃ
মন্দিরে নিত্যদিন পুজার্চনা হয়। সকালে বাল্যভোগ ও ¯œান পর্ব সম্পন্ন হয়। দুপুরে অন্নভোগ হয়। দুর দুরান্তের ভক্তগণ অন্নভোগের মানত করে। কেউবা মাচানের প্রথম লাউ বা কুমড়া মানত করে অন্নভোগের সময় এনে দেয়। সন্ধ্যায় আরতী হয় এবং ফলমুল, লুচি ইত্যাদি প্রাসাদে হিসেবে দেওয়া হয়। রাজার আমলে ছিল মাচানভরা কবুতর। কান্তজিউ মন্দিরের কবুতরের জ্বালায় স্থানীয় কৃষকদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতো। বিশেষ করে গম, কাউন ও সরিষা ক্ষেতে সবসময় পাহাড়া দিতে হতো। তখনকার আমলে ছিল গোয়াল ভরা গুরু। তাই ঠাকুরের পুজার্চনা হতো অত্যন্ত জাককমকপূর্ণভাবে। সে সময় দুধের স্বর দিয়ে তৈরি হতো ননী, ঘি, ছানাসহ বিভিন্ন সামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রী দিয়ে ঠাকুরের ভোগরাগ দেওয়া হতো। নিত্যদিনের পূজার্চনাগুলো মনে হয় এক একটি ধর্মীয় উৎসব। দেশ বিভাগের পর ১৯৫২ সালে এক বেদনা বিধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনাজপুর রাজবংশের সর্বশেষ রাজা মহারাজা জগদীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর স্মৃতিবিজড়িত দিনাজপুর ছেড়ে চলে যান কলকাতায়। রাজার দেশ ত্যাগ এর পরপরই মন্দিরের পূজার্চনায় ভাটা পড়ে যায়। চরম হতাশায় ভোগে মন্দিরের ভক্তমন্ডলী।
মন্দিরের বহির্গাত্র এবং ভগ্নমন্দির ঃ
মন্দির নির্মাণের পর মন্দির সংরক্ষণের জন্য রাজা মন্দিরের বহির্গাত্রে প্রাচীর নির্মাণ করেন। তবে অনেকে মনে করেন দোচালা বর্হিগাত্রটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের প্রথমার্ধে তৈরি করা হয়। কারণ কোম্পানি আমলের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশের টিনের ব্যবহার শুরু হয়। বর্হিগাত্রটির দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট এবং প্রস্ত ১২০ ফুট। বহির্গাত্রে অনেকগুলো ঘর আছে তার মধ্যে পূর্ব পাশের ঘরগুলো অফিস, ভাড়ার ঘর, রন্ধনশালা ও প্রসাদ বিতরণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উত্তর পার্শ্বে আছে ঠাকুর ঘর। পশ্চিম পাশে আছে গোয়াল ঘর। এক সময় মন্দিরে অনেক গরু ছিল। ছিল মাচান ভরা কবুতর। দোচালার অন্যান্য ঘরগুলোতে বিশ্রাম নেয় ভক্তবৃন্দ। মন্দিরের বাইরে উত্তর পাশে কালের সাক্ষী হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে ভগ্ন মন্দিরটি। এই ভগ্নমন্দিরটির আরেক নাম অর্চনা মন্দির। রাজা ও বৃন্দাবন থেকে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি নৌকাযোগে কান্তনগরে (শ্যামগড়) নিয়ে আসেন। রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ পুজার্চনার জন্য তাৎক্ষণিকভবে এই অর্চনা মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অর্চনা মন্দিরটি দেখতে শিব মন্দিরের মতো। তাই অনেকে শিব মন্দির বলে ভুল করেন। প্রতœতাত্তি¡কদের মতে এটি দ্বিতল বিশিষ্ট। কিন্তু অর্চনা মন্দিরের উপরিভাগ মানুষের অযতেœ অবহেলায় আর প্রাকৃতিক দুযোর্গে ভেঙ্গে পড়েছে। তাই আজ এটি দ্বিতল মন্দির।
তমাল বৃক্ষ ঃ
কান্তজিউ মন্দিরের উত্তর চত্বরে একটি তমাল বৃক্ষ ছিল। অতি দুলর্ভ তমাল গাছের কান্ড শাখা ও পাতা সব কৃষ্ণবর্ণ। এটি আকারে ছোট ঝুপসি গাছের মতো। তমাল বৃক্ষের ডালে বসেই শ্রীকান্ত বাঁশি বাজাতেন। আর শ্রীমতি রাধার মন বাঁশির সুরে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। অতি দুর্লভ কান্তজিউ মন্দিরের তমাল গাছটি ১৯৭৬ খ্রি. প্রচন্ড খড়ায় শুকিয়ে মারা যায়। তারপর সে স্থানেই আরও একটি তমাল গাছ লাগানো হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে অতি সম্প্রতি ২০০৪ খ্রি. জানুয়ারি মাসে আবার ও মন্দির চত্বরের সেই গাছটি মারা যায়। ২০০৪ খ্রি. ১৮ জুন তারিখে শ্রী গজেন্দ্রনাথের দেওয়া ৮ ফুট উচুঁ তমাল গাছের চারা রোপন করা হয়।
দোলবেদী ঃ
মন্দিরের সামান্য পূর্ব পাশে দোলবেদিটি অবস্থিত। প্রতিবছর অন্যান্য উৎসবের মতো দোলবেদীতে দোল উৎসব হয়।
রাসবেদী ঃ
মন্দিরের পশ্চিম পাশে রাসবেদীটি অবস্থিত। এখানে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রর্দশন করা হয়।
মন্দির নির্মাণের মিস্ত্রিগণ ঃ
যে কোন স্থাপত্যে যাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও সাধনায় নির্মিত হয় সেসব স্থপতি শিল্প কারিগর ও শ্রমিকদের নাম উল্লেখ থাকে না। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে তাজমহল। কান্তজিীউ মন্দিরের স্থপতি শিল্পী কারিগর ও শ্রমিকদের নাম উল্লেখ নেই। আছে শুধু পৃষ্ঠাপোষকদের নাম । কান্তজিউ মন্দিরের তিন কিলোমিটার দক্ষিণে নয়াবাদ গ্রামে ঐতিহাসিক নয়াবাদ মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদটি কান্তজিউ মন্দিরের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। কথিত আছে যে, কান্তজিউ মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে মুসলমান মিস্ত্রিগণ নয়াবাদ গ্রামে (মিস্ত্রিপাড়া মহল্লা) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। রাজার তত্ত¡াবধানে ও আর্থিক সহযোগিতায় মসজদিটি নির্মিত হয়। তার উদাহরণ কান্তজিউ মন্দিরের মত মসজিদের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণ। নয়াবাদ মসজিদটির নির্মাণকালের সময় ১৭৬০ খ্রি.। মসজিদের পাশে প্রধান মিস্ত্রি নিয়াজ এর কবর আছে। নিয়াজ মিস্ত্রির ডাক নাম কালুয়া মিস্ত্রি। রাজা মিস্ত্রিদের কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে কালুয়া মিস্ত্রিকে ১১ একর ৬ শতক জমি দান করেন।
রাজা প্রাণনাথের অন্যান্য কৃতিত্ব ঃ
রাজা প্রাণনাথ ১৬৮২ খ্রি. সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বকাল ছিল ৪০ বছর। তিনি শুধু দিনাজপুর রাজবংশেরই শ্রেষ্ঠতম রাজাই ছিলেন না তিনি ছিলেন তৎকালীন রাজাদের শিরমণি। রাজা প্রাণনাথ দিনাজপুর জেলায় অনেকগুলি খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য পূর্ত ও ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ করেন। তার এই কৃতিত্ব কর্মের জন্য তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার কৃতিত্ত¡গুলো হলো-
রাজা রামনাথের অন্যান্য কৃতিত্ব ঃ
রাজা প্রাণনাথ মারা যাওয়ার পর তার পোষ্যপুত্র রামনাথ ১৭২২ খ্রি. সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি তার পিতার অসমাপ্ত কান্তজিউ মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। ১৭৫২ খ্রি. মন্দিরটি উদ্ধোধন করেন। উক্ত মন্দিরটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অতুলনীয় স্থাপত্য ও অপরুপ টেরাকেটা মন্ডিত কীর্তিকর্ম। চির অ¤œান স্থাপত্যকলা অতুলনীয় শিল্প সৌকার্যে নির্মিত ইহার সমতুল্য এমন সুন্দর মন্দির শুধু বাংলাদেশ কেন সমগ্র ভারত বর্ষেই নেই। এমনকি সারা বিশ্বে এরকম সৌন্দর্যের মন্দির বিরল। রাজা রামনাথের অপর খ্যাতি সম্পন্ন কীর্তি সুবিশাল দিঘি রামসাগর। সাগর নয় তবুও নাম রামসাগর। চারদিকে ধু-ধু করা উদাসী গ্রামীণ প্রান্তর। বহুদুর দেখা যায় পল্লীজনপদ। মাটি ঢিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত অপরুপ রুপময় এই দিঘিটির সাধারণ দৃশ্যাবলী দেখতে বড়ই নয়নাভিরাম। এই দীঘির বিশালতলায় গভীরতায় শোভা সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। রাজা প্রাণনাথ গোবিন্দনগর অধিকারের পর রাজধানীর সাথে যোগাযোগের জন্য নৌকা চলাচলোপযোগী ২০ মাইল দীর্ঘ ৫০ ফুট প্রশস্ত একটি জলদাড়া খনন করেন। অতুলনীয় পূর্তকীর্তি এই জলদাড়ার নাম রামদাড়া। এছাড়া তিনি ১৭৫৪ সালে গোপালগঞ্জে জোড়ামন্দির, মমিদ্দির্বী মন্দির ১৭৪৬ খ্রি., দিঘনী গ্রামের কালিমন্দির ১৭৪৬ খ্রি., শুকেশ মন্দির, করদহ গ্রামের গোপাল মন্দির, ১৭৪৫ খ্রি. কাশিধামে শিব মন্দির, গৌরপতি মন্দির (মালদহ), রাজনগর মন্দির (মালদহ), রাধামাধবজীউর মন্দিরসহ অনেক ছোট বড় মন্দির নির্মাণ করেন।
ছবি
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৫-০৬-২৬ ২২:৪৮:০৩
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস